




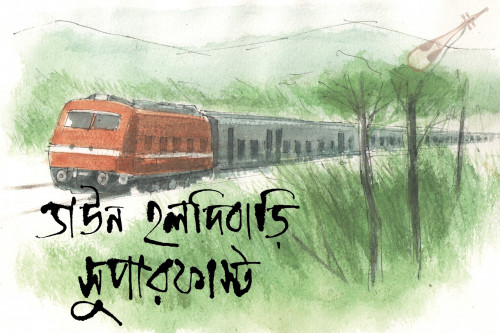


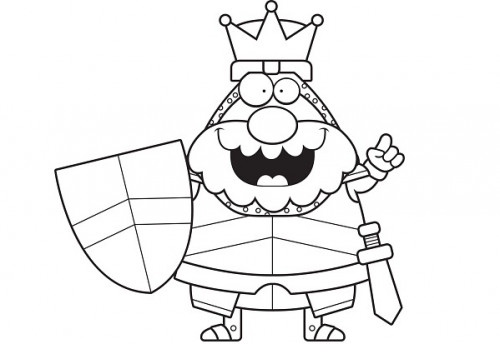


 а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට
а¶Єа¶ђаІНа¶ѓа¶Єа¶Ња¶ЪаІА බටаІНට

඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞-඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а•§ а¶Ча¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞බගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ьථ඙බаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х а¶РටගයаІНа¶ѓ а¶У ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ටඌ а¶ЕථаІНඃඌථаІНඃබаІЗа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞а•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Ьථа¶Ьඌටග ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶Х ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Еа¶Вප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙аІГඕа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ а¶Па¶ЦඌථаІЗ පඌඪථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Ьථ඙බаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶У ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Зටගයඌඪ а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ පගа¶≤аІН඙ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගа¶∞а¶У а¶РටගයаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶єаІА а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЕටаІАට ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ђа¶єа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ ටаІЛа¶∞аІНа¶Єа¶Њ ථබаІАа¶∞ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶Па¶З а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІВа¶∞аІНඐබගа¶ХаІЗ а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶У а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗа¶ґа•§ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප, а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶У а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶ња•§ ‘а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Чට а¶Еа¶∞аІНඕ ‘а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьඌටගа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ’а•§ а¶ђаІГа¶Яගප පඌඪථаІЗа¶∞ а¶ЕඐඪඌථаІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶єаІЯ аІІаІѓаІ™аІ≠ а¶ЦаІНа¶∞аІАа¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ аІІаІѓаІ™аІѓ а¶Єа¶Ња¶≤ ඙а¶∞аІНඃථаІНට ඪඌඁථаІНටаІНа¶∞ටඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ පඌඪගට а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІАаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а•§ аІІаІѓаІ™аІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІаІ® а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Ьа¶ЧබаІА඙аІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඙а¶Я ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞පඌඪථ а¶єа¶ЄаІНටඌථаІНටа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ аІ©аІ¶ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ аІІаІѓаІЂаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶єаІЯа•§
а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶≠а¶ђ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶≤аІЛа¶Ха¶ЊаІЯට а¶≠аІВ-а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ЬаІНа¶Юа¶Њ а¶У а¶Єа¶ЃаІЯаІЛ඙ඃаІЛа¶ЧаІА а¶ХаІНඣඁටඌаІЯ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча¶∞а¶ња¶ЈаІНආ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЄаІБа¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶ЧаІЬаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞ටගа¶ХаІВа¶≤ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ඕඌа¶Ха¶Њ ඪටаІНටаІНа¶ђаІЗа¶У а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ ඐග඙ථаІНථ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶Є а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа¶®а¶ња•§ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ පа¶ХаІНටගටаІЗа¶З а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЬ පඌඪථ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶У ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНඐටථаІНටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶Еа¶Єа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞-඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ ‘඙аІНа¶∞а¶Ња¶Ча¶ЬаІНа¶ѓаІЛටගඣ඙аІБа¶∞’ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶∞ ටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Єа¶ЃаІГබаІНа¶І а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а•§ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶≠а¶Ња¶∞ට, а¶єа¶∞а¶ња¶ђа¶Вප, පаІНа¶∞аІАඁබаІНа¶≠а¶Ња¶Ча¶ђаІО, а¶∞а¶ШаІБа¶ђа¶Вපඁ, а¶ЃаІОа¶Є ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЗ ‘඙аІНа¶∞а¶Ња¶Ча¶ЬаІНа¶ѓаІЛටගඣ඙аІБа¶∞’а¶Па¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ ඙аІАආаІЗ а¶ђа¶ња¶≠а¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ පඌඪථ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа¶З а¶Па¶З а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЕථаІБа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶Па¶З а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ ඙аІАආ а¶є’а¶≤ а¶Хඌඁ඙аІАආ, а¶∞ටаІНථ඙аІАආ, а¶ЄаІБа¶ђа¶∞аІНа¶£а¶™аІАආ а¶У а¶ЄаІМа¶Ѓа¶Ња¶∞඙аІАа¶†а•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶∞ටаІНථ඙аІАආаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට а¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶Ѓа¶ЩаІНа¶ЧаІЛа¶≤аІАаІЯ а¶ЖබගඐඌඪаІА а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа•§ а¶Па¶З а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶Жа¶∞аІНඃබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗපаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶З а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඐඪටග а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЙаІОа¶Єа¶Чට බගа¶Х බගаІЯаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьථа¶Ьඌටග а¶ђаІГа¶єаІО ‘а¶ђа¶∞аІЛ’ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶≠аІБа¶ХаІНа¶§а•§ а¶ђа¶∞аІЛа¶∞а¶Њ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Я඙аІВа¶∞аІНа¶ђ බපඁ පටа¶ХаІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ХаІНа¶ЈаІНඁ඙аІБටаІНа¶∞ ථබаІЗа¶∞ ඙ඌаІЬаІЗ ඐඪටග а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶Єа¶є а¶ЙටаІНටа¶∞-඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђа¶∞аІЛ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘а¶ЬаІНа¶Юඌථ’ а¶ђа¶Њ ‘а¶єаІБа¶Бප’а•§ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘ඁඌථаІБа¶Ј’а•§ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ча¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ‘а¶ЃаІЗа¶Ъ’ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ ‘а¶Ѓа¶ња¶Ъ’ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ѓа¶ња¶Ъ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ъа¶њ ථබаІАа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶∞аІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶ња¶Ъ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘ඁඌථаІБа¶Ј’а¶У а¶ђа¶ЯаІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ ‘а¶Ѓа¶ња¶ЬаІЛ’ (а¶Ѓа¶њ—ඁඌථаІБа¶Ј, а¶ЬаІЛ—а¶Йа¶Ба¶ЪаІБа¶ЄаІНඕඌථ) а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Йа¶Ба¶ЪаІБа¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђа¶Њ ඙а¶∞аІНඐටаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја•§ ටаІЗඁථа¶З ‘а¶єа¶Ња¶ЬаІЛ’ (а¶єа¶Њ—а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶њ, а¶ЬаІЛ—а¶Йа¶Ба¶ЪаІБа¶ЄаІНඕඌථ) а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ ඥගඐගа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ха¶Ња¶∞аІА ඁඌථаІБа¶Ја•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ‘а¶Ѓа¶ња¶Ъа¶Њ’ (а¶Ѓа¶њ—ඁඌථаІБа¶Ј, а¶Ъа¶Њ—ඪථаІНටඌථ)а•§ а¶ђа¶∞аІЛа¶Ха¶ња¶Ъа¶Њ ඁඌථаІЗ а¶ђа¶∞аІЛබаІЗа¶∞ ඪථаІНа¶§а¶Ња¶®а•§
а¶Рටගයඌඪගа¶Х ඁටඌථаІБа¶ѓа¶ЊаІЯаІА а¶єа¶∞ගබඌඪ ඁථаІНа¶°а¶≤ (а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Њ ඁථаІНа¶°а¶≤)-а¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌටඌ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Ча¶£аІНа¶ѓ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА඙аІНа¶∞඲ඌථ, а¶Ъа¶ња¶Хථඌ ඙а¶∞аІНඐටаІЗа¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Па¶Х а¶≠аІВ-а¶ЦථаІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Ха•§ а¶єа¶∞ගබඌඪ ඁථаІНа¶°а¶≤аІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ‘බа¶∞а¶ЩаІНа¶Ча¶ђа¶Вපඌඐа¶≤аІА’, а¶ЦаІЬа¶Ч ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶ђа¶Вපඌඐа¶≤аІА, а¶ЧථаІНа¶Іа¶∞аІНа¶ђ ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶ђа¶Вපඌඐа¶≤аІА, а¶єа¶∞а¶ХඌථаІНට а¶ђаІЬаІБаІЯа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Еа¶Єа¶Ѓ-а¶ђаІБа¶∞аІБа¶ЮаІНа¶ЬаІА ඕаІЗа¶ХаІЗа•§
а¶Па¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕබаІБа¶∞аІЗа¶З а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕගට ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට පගඐඪаІНඕඌථ ‘а¶Ьа¶≤аІН඙аІЗප’а•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ පගඐаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථ а¶Па¶Яа¶ња•§ а¶ЕටаІАටаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ња¶ХаІАа¶∞аІНа¶£ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА඙ටග а¶єа¶∞ගබඌඪ ඁථаІНа¶°а¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඃබගа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶Жබගථගඐඌඪ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶∞ටаІНථ඙аІАආаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶Чට а¶ђа¶ња¶ЄаІНටගа¶∞аІНа¶£ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Вප ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Цගට ‘а¶Ъа¶ња¶Хථඌ’аІЯа•§ а¶єа¶∞ගබඌඪ ඁථаІНа¶°а¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶є а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Х а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Єа¶∞аІНබඌа¶∞ ‘а¶єа¶Ња¶ЬаІЛ’-а¶∞ බаІБа¶З а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ ‘а¶єа¶ња¶∞а¶Њ’ а¶У ‘а¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ’-а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ЧаІМа¶єа¶Ња¶Яа¶њ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞-඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶Ьа¶ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ча¶∞аІНа¶≠аІЗ ‘а¶ЪථаІНබථ’, а¶єа¶ња¶∞а¶Ња¶∞ ඪථаІНටඌථ ‘ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є’ а¶У ‘පගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є’ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞යථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ ඙а¶∞аІЗ ‘ඁබථ’ ථඌඁаІЗ а¶Па¶Х ඙аІБටаІНа¶∞ ඪථаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ බаІЗа¶®а•§ а¶єа¶∞ගබඌඪ ඁථаІНа¶°а¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Ъа¶Ња¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶∞аІНඐඌ඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђаІБබаІН඲ගඁඌථ, а¶ђа¶≤ඐඌථ а¶У а¶Єа¶Ња¶єа¶ЄаІА а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶єа¶∞ගබඌඪаІЗа¶∞ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Њ а¶ђаІЗප а¶ђаІЬ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ පඌඪථ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබථ а¶Ха¶∞а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Й඙ඃаІБа¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ а¶ЕථаІБа¶∞аІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶ЪථаІНබථа¶ХаІЗ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶ђа¶Єа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓаІЗа•§ а¶єа¶∞ගබඌඪ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶∞ а¶Па¶З а¶Жඐබඌа¶∞ а¶ПаІЬඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ьа¶ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඪථаІНටඌථ ඁබථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗ ථගයට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЪථаІНබථ а¶ђа¶Єа¶≤аІЗථ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ පඌඪථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ බගаІЯаІЗа¶З а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ථටаІБථ а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶є’а¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶Цඌථа¶Ха¶Ња¶∞ ‘а¶∞а¶Ња¶Ьපа¶Х’-а¶Па¶∞ а¶Ча¶£а¶®а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯа•§ а¶ЪථаІНබථ аІІаІЂаІІаІ¶ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІЂаІ®аІ® а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶∞аІЛа¶Ча¶ЧаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶єаІЯаІЗ ඙а¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶Чඁථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§
а¶ЪථаІНබථаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ ඙а¶∞ аІІаІЂаІ®аІ® а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶ђа¶Єа¶≤аІЗථ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єа•§ ටගථග а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ђа¶єаІБබаІВа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටගථගа¶З а¶ХаІЛа¶Ъа¶Ьඌටගа¶ХаІЗ а¶Х’а¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗථ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗаІЯ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІАа•§ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЛаІЯа¶Њ ථබаІА ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶ђа¶∞аІЛ ථබаІА ඙а¶∞аІНඃථаІНට ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶Ъа¶ња¶Хථඌ ඙а¶∞аІНඐට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ь඲ඌථаІА ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗථ а¶Жа¶≤ග඙аІБа¶∞බаІБаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶≤а¶ЧаІБаІЬа¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶єа¶ња¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа•§ ටගථග ‘а¶ЖඁටаІЗපаІНа¶ђа¶∞’ а¶Й඙ඌ඲ග а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶З පගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є ‘а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞’а¶Па¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ ඙аІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Й඙ඌ඲ග а¶є’а¶≤ а¶∞а¶ЊаІЯа¶ХаІОа•§ පගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶∞аІНඃඌබඌ ඙аІЗа¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටගථග а¶єа¶≤аІЗථ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථඪаІНඕ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь а¶Па¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНඐ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНа¶§а•§ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶є’а¶≤ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶Ња¶≠а¶ња¶ЈаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶З а¶∞а¶ЊаІЯа¶ХаІОа¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЫටаІНа¶∞а¶Іа¶∞ а¶єа¶ђаІЗа¶®а•§ ටඐаІЗ පගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶ХаІНඣඁටඌа¶З а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ьа¶≤඙ඌа¶За¶ЧаІБаІЬа¶њ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЙаІО඙ටаІНа¶§а¶ња•§
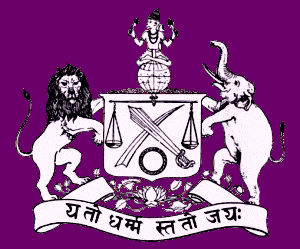
ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Хඕඌа¶Яа¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶П а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶°. а¶єа¶Ња¶£аІНа¶Яа¶Ња¶∞ аІІаІЃаІ≠аІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ‘а¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶Єа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Я а¶Еа¶Ђ а¶ђаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’-а¶Па¶∞ බපඁ а¶ЦථаІНа¶°аІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ‘඙а¶ЮаІНа¶Ъබප පටа¶ХаІЗа¶∞ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶єа¶Ња¶ЬаІЛ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ЄаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ බаІМයගටаІНа¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶Єа¶єа¶Ъа¶∞а¶ђа¶∞аІНа¶Ч а¶Єа¶є යගථаІНබаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ѓа¶Ха¶Ња¶≤ගථ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІНа¶Ѓа¶£а¶Ча¶£ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶ЖබගඐඌඪаІА ඙аІНа¶∞඲ඌථаІЗа¶∞ ථඌඁаІЗ а¶ђа¶Вප а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶∞аІАටගа¶Яа¶њ а¶Па¶З а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌ ඙ඌаІЯа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶ђа¶Вපа¶Ьඌට а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Ча¶£ а¶ХаІЛа¶Ъ ථඌඁ ඙а¶∞ගටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶Х’а¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА ථඌඁ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§’ а¶ЬඌටаІАаІЯ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶ЄаІБථаІАටගа¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ЯаІНа¶ЯаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶ЊаІЯ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ යගථаІНබаІБа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶У а¶Єа¶Ва¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶Ха¶∞а¶£ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞аІВ඙аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ බගටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ђаІБа¶Хඌථථ а¶єаІЗа¶Ѓа¶≤аІНа¶Яථ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ, а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ඙аІВа¶∞аІНඐටථ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗа¶∞а¶З а¶Жබග а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶Па¶ђа¶В а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жබග ඁඌථඐа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶ЄаІБа¶Єа¶≠аІНа¶ѓ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Жබග ඁඌථඐа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ХаІЛа¶Ъ а¶У а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНඕа¶Ха¶∞аІВ඙аІЗ а¶ђа¶ња¶ђаІЗа¶Ъගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶Па¶З а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථඃඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶У а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗ а¶≠ගථаІНථටඌ, ඐගපගඣаІНа¶Яටඌ а¶Еа¶∞аІНа¶ЬථаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕ а¶єаІЯа•§’ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, ‘а¶ЙаІОа¶Єа¶Чට බගа¶Х බගаІЯаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶є’а¶≤ а¶Еථඌа¶∞аІНа¶ѓ а¶ЬඌටගඪඁаІНа¶≠аІВа¶§а•§ а¶єа¶Ња¶ЬаІЛ’а¶∞ ඙аІМටаІНа¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є, ටඌа¶Ба¶∞ а¶Жа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶У а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Ьථа¶Ча¶£ යගථаІНබаІБа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ХаІЛа¶Ъ ථඌඁ ඙а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Х’а¶∞аІЗ ‘а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶ВපаІА’ ථඌඁ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ The name Rajbansi, which literally means ‘Royel Race’, is adopted by cultivators and respectable man.’
ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є аІІаІЂаІ®аІ® ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІЂаІ©аІ© а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶Жа¶ЄаІАථ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗа¶∞ බඌඐගබඌа¶∞ а¶єа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ ටගථ ඙аІБටаІНа¶∞а•§ ථа¶∞а¶Єа¶ња¶Ва¶є, ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶У පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ьа•§ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ь ‘а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ’ ථඌඁаІЗ а¶Еа¶Іа¶ња¶Х ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђаІАа¶∞ а¶У а¶Єа¶Ѓа¶∞ ඐගබаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЕටаІНඃථаІНට ඙ඌа¶∞බа¶∞аІНපаІАа•§ а¶Хඕගට а¶ѓаІЗ ටගථග පටаІНа¶∞аІБ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Эа¶Ња¶Б඙ගаІЯаІЗ ඙аІЬටаІЗථ а¶Ъа¶ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІНඣග඙аІНа¶∞ටඌаІЯа•§ ටඌа¶З ‘а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ’ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶єа¶≤аІЗථ а¶ЗටගයඌඪаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶У а¶ЙටаІНටа¶∞а¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј පаІНа¶∞බаІН඲ඌඐථට а¶ЪගටаІНටаІЗ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶Жа¶ЄаІАථ а¶єа¶≤аІЗථ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£а•§ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶Вයඌඪථ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටග а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Хඌයගථග ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶єаІЗа¶∞ ඙а¶∞ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶Єа¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶Х а¶ЖපаІАа¶∞аІНඐඌබ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞а¶£ а¶ЄаІН඙а¶∞аІНප а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Па¶≤аІЗ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶ХаІЗ ‘а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ѓа¶єа¶ња¶ЈаІА а¶≠а¶ђа¶Г’ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жපගඪ а¶Ьඌථඌа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђаІБබаІН඲ගඁටаІА ඙аІБටаІНа¶∞а¶ђа¶ІаІВ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА а¶Єа¶ња¶Вයඌඪථ ථඌ ඙аІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІА а¶Х’а¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ѓа¶єа¶ња¶ЈаІА а¶єа¶ђ! ටඌа¶Ба¶∞ а¶Хඕඌ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗа¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ යඌටаІЗ පඌඪථа¶≠а¶Ња¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђаІЬ඙аІБටаІНа¶∞ ථа¶∞а¶Єа¶ња¶Ва¶є ටඌ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගа¶≤аІЗа¶®а•§ ථа¶∞а¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЦаІНඃඌට а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶Х а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, According to Gait, Narasingha seized the throne after Biswa Singha but Naranarayan drove him out and he fled to Bhutan and founded a kingdom there.
а¶Па¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЕථඌаІЯа¶Ња¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞බаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯථ а¶У පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ьа•§ ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶Жආඌа¶∞аІЛа¶Ьථ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶ЈаІА а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඪථаІНටඌථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жආඌа¶∞аІЛа¶Яа¶ња•§ බа¶∞а¶В а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ђа¶Вපඌඐа¶≤аІАටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ
а¶єаІЗඁ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Њ ඙බаІНඁඌඐටаІА බаІБа¶З а¶ђа¶∞ථඌа¶∞аІА
а¶ЧаІМа¶∞ බаІЗප а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටඌа¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶ЗථаІНට а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶њ а•§а•§
а¶єаІЗඁ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Њ යථаІНටаІЗ ඃගටаІЛ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Йට඙ථ
а¶ЧථගаІЯа¶Њ බගа¶≤ථаІНට ථඌඁ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£а•§а•§
඙බаІНඁඌඐටаІА යථаІНටаІЗ а¶ѓа¶ња¶ЯаІЛ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Йට඙ටග
ටඌථ ථඌඁ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ь а¶ЦаІЗа¶≤ථаІНට а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටග а•§а•§
а¶ХаІЛа¶ЪаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶∞а¶Ња¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГට а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ЬаІНа¶ЮඌථаІАа•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට පගа¶ХаІНඣගට а¶Па¶З බаІБ’а¶≠а¶Ња¶З ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶ЙථаІНථටගа¶∞ පගа¶ЦаІЬаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගටаІЗа¶У ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Еඐබඌථ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ аІІаІЂаІЂаІЂ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗ а¶Еа¶єа¶Ѓ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ථа¶∞-ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶Ъගආගа¶Яа¶ња¶З а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ЧබаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ථගබа¶∞аІНපථ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪඐගබа¶Ча¶®а•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Ъගආගа¶Яа¶њ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња•§
а¶Па¶З ඙ටаІНа¶∞а¶ХаІЗа¶З а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙ථаІНධගටа¶Ча¶£ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ЧබаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Єа¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З ඙ටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶У ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Яа•§
“а¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටග а¶Єа¶Ха¶≤ බගа¶ЧථаІНට а¶Ха¶£а¶§а¶Ња¶≤а¶Њ а¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Єа¶ЃаІАа¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගඕග а¶Ѓа¶Ха¶∞ а¶єа¶∞а¶єа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶Хඌප а¶ХаІИа¶≤а¶Ња¶Є ඙ඌථаІНа¶°аІВа¶∞а¶Ј පаІЛа¶∞а¶Њ පගඐගа¶∞а¶Њ а¶ЬගටаІНටаІНа¶∞а¶њ ඙ගඣаІНа¶Я ඙ටගබප ටа¶∞а¶ЩаІНа¶ЧගථаІА а¶Єа¶≤а¶ња¶≤ ථගа¶∞аІНа¶ЃаІНа¶Ѓа¶≤ ඙ඐගටаІНа¶∞ а¶Ха¶≤аІЗа¶ђа¶∞ а¶ІаІАа¶Ја¶£а¶ІаІАа¶∞ а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓаІНඃබඌ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ බගа¶ХаІНа¶Ха¶Њ ඁගථаІАа¶ЄаІАаІЯඁඌථ а¶ЧаІБа¶£а¶Єа¶®аІНටඌථ පаІНа¶∞аІА පаІНа¶∞аІА а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶Чථඌа¶∞а¶ЊаІЯථ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ь ඙аІНа¶∞а¶ЪථаІНа¶° ඙аІНа¶∞ටඌ඙аІЗа¶ЈаІБа•§
а¶≤аІЗа¶Цථа¶В а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Юа•§ а¶Пඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІБපа¶≤а•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІБපа¶≤ ථගа¶∞ථаІНටа¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Юа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Еа¶Цථ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪථаІНටаІЛа¶Ја¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶Х ඙ටаІНа¶∞ඌ඙ටаІНа¶∞а¶њ а¶ЧටඌаІЯට а¶єа¶За¶≤аІЗ а¶Йа¶≠аІЯඌථаІБа¶ХаІВа¶≤ ඙аІНа¶∞аІАටගа¶∞ а¶ђаІАа¶Ь а¶Еа¶ЩаІНа¶ХаІБа¶∞ගට а¶єа¶ЗටаІЗ а¶∞а¶єаІЗа•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІНටඐаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђа¶∞аІНබаІН඲ගටඌа¶Х ඙ඌа¶З ඙аІБа¶ЈаІН඙ගට а¶ЂаІБа¶≤ගට а¶єа¶За¶ђаІЗа¶Ха•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗටаІЗ а¶Жа¶Ыа¶њ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞а¶У а¶Па¶ЧаІЛа¶Я а¶Ха¶∞аІНටඐаІНа¶ѓ а¶Йа¶Ъа¶њаІО а¶єаІЯ ථඌ а¶Ха¶∞ ටඌа¶Х а¶Ж඙ථ а¶Ьа¶Ња¶®а•§ а¶Еа¶Іа¶ња¶Х а¶Ха¶њ а¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶Ѓа•§ ඪටаІНඃඌථථаІНබ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА а¶∞а¶Ња¶ЃаІЗපаІНа¶ђа¶∞ පа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ а¶Ха¶Ња¶≤а¶ХаІЗටаІБ а¶У а¶ІаІБа¶Ѓа¶Њ ඪබаІНබඌа¶∞ а¶ЙබаІНබථаІНа¶° а¶Ъа¶Ња¶ЙථගаІЯа¶Њ පаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶Ња¶З а¶За¶Ѓа¶Ња¶Х ඙ඌආඌа¶ЗටаІЗа¶Ыа¶њ ටඌඁа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶Эа¶њаІЯа¶Њ а¶Ъගටඌ඙ ඐගබඌаІЯ а¶¶а¶ња¶ђа¶Ња•§
а¶Е඙а¶∞ а¶Йа¶Ха¶ња¶≤ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ШаІБаІЬа¶њ аІ®а¶ІаІЗථаІБ аІІа¶ЪаІЗа¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶ЃаІОа¶Є аІІа¶ЬаІЛа¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶Ъ аІІа¶Ьа¶Ха¶Ња¶З аІІа¶Єа¶Ња¶∞а¶њ ಀඕඌථ а¶Па¶З а¶Єа¶Ха¶≤ බගаІЯа¶Њ а¶Ча¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞аІБ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶Эа¶њ а¶Ха¶З ඙ඌආඌа¶За¶ђаІЗа¶Ха•§ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗ ඪථаІНබаІЗප а¶ЧаІЛа¶Ѓа¶ЪаІЗа¶В аІІа¶Ыа¶ња¶Я аІЂа¶Ша¶Ња¶Ча¶∞а¶њ аІІаІ¶а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞ ಮಶපаІБа¶ХаІНа¶≤а¶Ъа¶Ња¶Ѓа¶∞ аІІаІ¶а•§ а¶Зටග පа¶Ба¶Х аІІаІ™аІ≠аІ≠ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Жа¶Ја¶ЊаІЭа•§”
ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ХаІЗ බаІБа¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶Вප ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶Е඙а¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч ඙аІЗа¶≤аІЗථ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ьа•§ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶ѓа¶Њ а¶Єа¶Ва¶ХаІЛපаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඁයඌථථаІНබඌ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ВපаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ва¶ХаІЛපаІЗа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶Ча•§ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶ња¶Х а¶У а¶ђаІАа¶∞ а¶ѓаІЛබаІНа¶Іа¶Ња•§ ටගථග ටаІЬගබаІНа¶ЧටගටаІЗ පටаІНа¶∞аІБа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ЬаІЯ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ШаІЛаІЬа¶Ња¶∞ ඙ගආаІЗ а¶ЪаІЗ඙аІЗ ‘а¶Ъа¶ња¶≤аІЗа¶∞’ ඁට а¶≤а¶Ња¶Ђ බගаІЯаІЗ а¶Іа¶∞а¶≤а¶Њ ථබаІА ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁ а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶єаІЯ а¶ђа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ЯаІЯаІЗථඐග а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶ЗටගයඌඪаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ ටගථа¶Ьථ а¶ђаІАа¶∞аІЗа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ පаІБа¶ХаІНа¶≤а¶ІаІНа¶ђа¶Ьа•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ බаІБа¶Ьථ ථаІЗ඙а¶≤а¶њаІЯථ а¶ђаІЛථඌ඙ඌа¶∞аІНа¶Я а¶У а¶ЫටаІНа¶∞඙ටග පගඐඌа¶ЬаІАа•§
ඐගපаІНа¶ђа¶Єа¶ња¶Ва¶є බаІБа¶За¶≠а¶Ња¶За¶ХаІЗ බаІБа¶З а¶Еа¶ВපаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ බගа¶≤аІЗථ а¶ђа¶ЯаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£а•§ а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶єа¶≤аІЗථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶∞а¶ХаІБපа¶≤аІА а¶ЄаІЗа¶®а¶Ња¶™а¶§а¶ња•§ а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗ ඙а¶∞а¶Ња¶Ьගට а¶єаІЯаІЗ ඁථග඙аІБа¶∞, а¶ЬаІЯථаІНටගаІЯа¶Њ, ටаІНа¶∞ග඙аІБа¶∞а¶Њ, පаІНа¶∞аІАа¶єа¶ЯаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Њ ඐපаІНඃටඌ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶З а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯа•§ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђаІЗ а¶ђа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІАඁඌථаІНටඐа¶∞аІНටаІА а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶ЃаІЗ ටаІНа¶∞а¶ња¶єаІБට а¶Па¶ђа¶В а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ ටගඐаІНඐට ඕаІЗа¶ХаІЗ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£аІЗ а¶ШаІЛаІЬа¶Ња¶Ша¶Ња¶Я ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЄаІАඁඌථඌ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ‘ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£’ ථඌඁаІЗ а¶ЄаІЛථඌ а¶У а¶∞аІВ඙ඌа¶∞ а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶Ха¶∞аІЗථ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£а•§ а¶Па¶З а¶ЃаІБබаІНа¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶≠аІВа¶ЯඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඐගපඌа¶≤ а¶Па¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ђаІЗපගබගථ а¶ЄаІНඕඌаІЯаІА а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ ඪ඙аІНටබප පටඌඐаІНබග ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Еඐථටග а¶Ша¶ЯටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа•§
а¶Ъа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ ඙а¶∞ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶∞а¶ШаІБබаІЗа¶ђ а¶∞а¶Ња¶Ь а¶Єа¶ња¶Вයඌඪථ බඌඐග а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ ථа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐබаІНබපඌටаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶≠а¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ බаІБа¶Яа¶њ ඙аІГඕа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯаІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶≤а¶єаІЗ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£аІЗ а¶ђа¶ња¶ІаІНа¶ђа¶ЄаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЃаІБа¶Ша¶≤ а¶У а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ බаІБ’඙ඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£ а¶ХаІЛа¶Ъа¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගයට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶ња•§ а¶Е඙а¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶Яඌථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶У а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯа•§ а¶Уබගа¶ХаІЗ а¶ђаІИа¶ХаІБථаІНආ඙аІБа¶∞ ඙аІГඕа¶Х а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶∞аІВ඙аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶ШаІЛа¶Ја¶£а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ь а¶ЃаІЛබථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶≠аІБа¶ЯඌථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ ටඌ а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶Ь а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඙аІБථа¶∞а¶ЊаІЯ а¶≠аІВа¶ЯඌථаІЗа¶∞ а¶Еа¶ІаІАථаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ ථඌඁаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗථ, а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶ХаІНඣඁටඌ ඕඌа¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶Яඌථ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ යඌටаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶≠а¶∞а¶£а¶™аІЛа¶Ја¶£ ඙аІЗටаІЗа¶®а•§
а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶ХаІЛа¶ЪаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЧаІЛ඙ථаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ЪаІБа¶ХаІНටග а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ ඙аІБථа¶∞аІБබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞බ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗа¶З а¶Ъа¶Ња¶∞පаІЛ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶≠аІМа¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еඐඪඌථ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬබаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞බ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓа¶∞аІВ඙аІЗ а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, а¶єа¶∞аІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, ථа¶∞аІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, ථаІГ඙аІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, а¶ЬගටаІЗථаІНබаІНа¶∞ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£, а¶∞а¶ња¶ЬаІЗථаІНа¶Єа¶њ а¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Єа¶ња¶≤ а¶Па¶ђа¶В а¶Ьа¶ЧබаІНබаІА඙аІЗථаІНබаІНа¶∞ ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£ а¶Єа¶ња¶ВයඌඪථаІЗ а¶Жа¶ЄаІАථ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§
аІІаІѓаІ™аІѓ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබаІЗа¶∞ аІІаІ® а¶ЄаІЗ඙аІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶За¶ЙථගаІЯථаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶єаІЯа•§ а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖබаІЗපа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІНа¶ѓа¶≠ඌටඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶≤аІЛ඙ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ аІІаІѓаІЂаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ аІІ а¶ЬඌථаІБаІЯа¶Ња¶∞а¶њ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ња¶Ѓа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІВа¶ХаІНට а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ аІІаІЂаІІаІ¶ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІ≠аІ≠аІ© а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЃаІЛа¶Я аІ®аІђаІ© а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶∞බ ඁගටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓ а¶∞аІВ඙аІЗ аІІаІ≠аІ≠аІ© а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІѓаІ™аІѓ а¶ЦаІНа¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНබ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЃаІЛа¶Я аІІаІ≠аІђ а¶ђаІОа¶Єа¶∞, а¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞පаІЛ а¶Ъа¶≤аІНа¶≤ගප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Еඐඪඌථ а¶Ша¶ЯаІЗа•§ а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙аІНа¶∞а¶Ьа¶Ња¶ђаІОа¶Єа¶≤, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІА а¶У а¶Іа¶∞аІНඁ඙а¶∞а¶ЊаІЯа¶£а•§ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග ඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶Ч ථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§
а¶ХаІЛа¶Ъ а¶∞а¶Ња¶ЬටථаІНටаІНа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶ЃаІЯ а¶У а¶Ша¶ЯථඌඐයаІБа¶≤а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶ЊаІЬаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞පаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶Зටගයඌඪ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£аІАаІЯа•§ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ва¶ХаІНඣග඙аІНට а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶Яа¶њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ථගа¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІЗа•§ а¶Жа¶ЧаІНа¶∞а¶єаІАа¶∞а¶Њ а¶П а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටаІГට а¶ЬඌථටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗ ‘а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ’ ඙аІБа¶ЄаІНටа¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶У ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Па¶З а¶ХаІЗටඌඐа¶Яа¶њ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Рටගයඌඪගа¶Х а¶ЖඁඌථඌටаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗа¶¶а•§ а¶Па¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞а¶ђаІЛ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Х а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯа•§
а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓ а¶∞а¶ЪථඌපаІИа¶≤а¶њ а¶У а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථඌаІЯ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථටаІНа¶ђаІЗа¶∞ බඌඐග а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗа•§ а¶ХаІБපඌථ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Чඌථ, а¶ђа¶ња¶Ја¶єа¶∞а¶њ, බаІЛටа¶∞ඌබඌа¶Ща¶Њ, а¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶≤, а¶ЪථаІНධගථඌа¶Ъ, а¶Хඌටග඙аІВа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Чඌථ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ХаІЛа¶Ъа¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶ЊаІЯа•§ බගථයඌа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІБපඌථ ඙ඌа¶≤а¶Ња¶Чඌථ ටаІЛ а¶ЕථඐබаІНа¶ѓа•§ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶єаІБබаІБа¶Ѓ බаІЗа¶У, а¶Ьа¶Ща¶Чඌථ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶≤аІЛа¶Хථඌа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග ඐගබа¶ЧаІНа¶І а¶Ьථа¶ХаІЗа¶У а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа•§
(а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІА а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team