



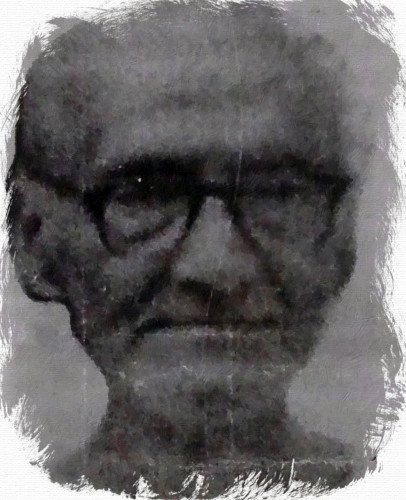




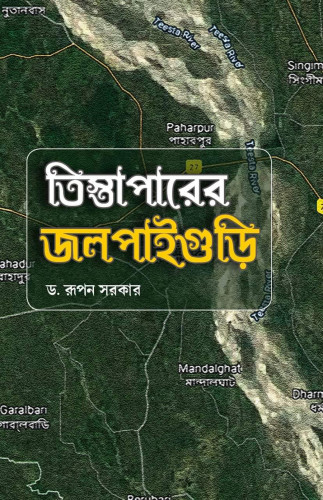








 শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
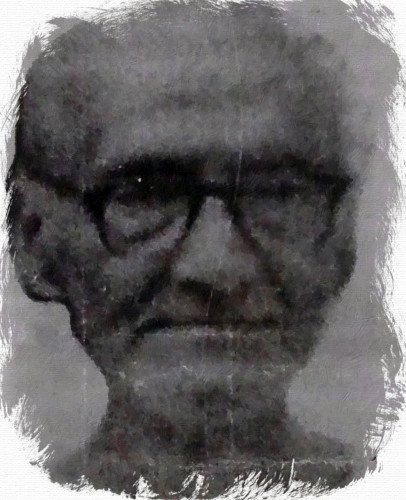
বান্ধব নাট্য স্থাপিত হলো। তার মঞ্চ তৈরি হলো ১৯২৪-এ। সেই মঞ্চে সদস্যরা প্রথম নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ করেছিলেন ‘আলমগীর’। ক্ষিরোদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই পালা সেকালের জনপ্রিয় পালা। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় জীবনও শুরু এই নাটক দিয়ে। টাউনের ইতিহাস নিয়ে যেমন সিরিয়াস চর্চা আছে, তেমনই গুজবেরও অন্ত নেই। এই রকম একটি চলতি গুজব হলো বান্ধব নাট্যের মঞ্চ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিশিরবাবু নাকি তাঁর দলবল নিয়ে সাতদিন টাউনে থেকে ওই মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন।
কিন্তু এ নিতান্ত গুজবই।
তবে শিশিরবাবু না এলেও অনামি-অখ্যাত পেশাদার যাত্রা-নাটকের দল অবশ্য আর্যনাট্যের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নাটক করত। বলতে গেলে করলা নদীর পাড়ে থাকা এই আর্যনাট্যই ছিল ওইসব পেশাদার দলগুলির টার্গেট। আর্যনাট্যের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে থাকত। এইসব দলের অভিনেতাদের ওপর কড়া নজর রাখতেন আর্যনাট্যের সদস্যরা। নজর রাখার কারণ অবশ্য মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করা ছেলে অভিনেতারা। তেমন কোন প্রতিভাবান ‘সখী’র সন্ধান পেলে নিজেদের দলে টেনে নিতে বিন্দুমাত্র দেরি করতেন না তাঁরা। শোনা যায় এই কাজে আর্যনাট্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং বাইরে থেকে আসা দলের অধিকারীরা এ নিয়ে বেশ টেনশনে থাকতেন।
শিশির ভাদুড়ী আসেন নি। সে কালে কলকাতা থেকে জলপাইগুড়িতে এসে নাটক করার সম্ভাবনাও তাঁর ছিল না। তবে কলকাতার নাটকের অনুকরণেই চলত টাউনের নাট্যচর্চা। আর যিনি কলকাতায় শিশিরবাবুর দলে নাটক করার অভিজ্ঞতা নিয়ে টাউনে এসে স্থানীয় নাট্যচর্চাকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নাম ছিল গণেশচন্দ্র রায়।
সত্যি কথা বলতে টাউন জলপাইগুড়ির কোনও ঐতিহ্য ছিল না। সে তো ছিলই না কখনো ইতিহাসে। ইংরেজদের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এই টাউনে সংস্কৃতি চর্চা অতি দ্রুত বিকশিত হলেও ঐতিহ্য বলতে যা বোঝায়, সেটা থেকে সে বঞ্চিত। মুর্শিদাবাদ, কুচবিহার কি কৃষ্ণনগরের মত তার ছিল না কোন মধ্যযুগীয় উত্তরাধিকার। তার ইতিহাস শুরু হয়েছে আধুনিক যুগ দিয়েই। কলকাতার মত। গোড়ায় এই টাউনের সংস্কৃতি ছিল কলকাতার ‘বাবু কালচার’-এর এক দুর্বল সংস্করণ, যেখানে ইংরেজ এবং ব্যবসায়ী, মুৎসুদ্দি, চা-বাগান মালিক, ইংরেজি জানা কেরানী আর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ভাগ্যান্বেষীর ভিড়। যেহেতু রেল যোগাযোগের কারণে কলকাতা মাত্র এক রাতের দূরত্ব তাই সেকালের ভারতীয় রাজধানীর তাপোত্তাপ পৌঁছোতে দেরি হত না।
আর্যনাট্য, সম্ভবত গোড়ার দিকে সেই বাবু কালচারের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। তাঁদের ঝোঁক ছিল সেইসব নাটক অভিনয় যা নিরাপদ। ইংরেজদের অস্বস্তির কারণ নয়। তারা কখনোই ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায় না--- এমনকি টাউনে যখন স্বদেশী আন্দোলন তুঙ্গে, যখন স্বদেশী করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হচ্ছেন বহু মানুষ, যখন তাঁদের কাউকে কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ইংরেজরা ধরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসছে গরুমারার গভীর অরণ্যে --- তখনো নয়।
গণেশচন্দ্র এর মধ্যেই চেষ্টা করেছিলেন নতুন কিছু করতে। তাঁর জন্ম দিনহাটায়। পিতা ছিলেন কুচবিহারের রাজকর্মচারী কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে তিনি চলে আসেন জলপাইগুড়ি, যেখানে তাঁর দাদা চাকরি করতেন। ম্যাট্রিক পাসের পর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতাতেই যেতে হত তখন। তিনিও যান এবং গিয়ে জড়িয়ে পড়েন সেখানকার উত্তেজনাপূর্ণ নাট্যপরিমন্ডলে। সেকালের বহু নামযাদা নাট্যব্যক্তিত্বের সাথে অভিনয়ের সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। এরপর সেখানে থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি আবার ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি। আর্যনাট্য তাঁকে পেয়ে উপকৃত হয়েছিল, কিন্তু গণেশচন্দ্র তৃপ্ত হন নি। ওইসব নিরামিষ নাটকে তাঁর মন ভরছিল না। ফলে একটা সময়ের পর তিনি ছেড়ে দিলেন আর্যনাট্য।
বান্ধব নাট্যেও ছিল একই ধরনের নাট্যচর্চা। কাজেই গণেশচন্দ্রকে অপেক্ষা করতে হলো। এরপর তিনি গণনাট্যের জড়িয়ে পড়বেন। কিন্তু সে ভিন্ন কাহিনী।
বস্তুত প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পঞ্চাশ বছর জলপাইগুড়ি টাউনের সাংস্কৃতিক পরিচয় বলে কিছু ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে টাউনে বেশ কিছু পরিবার বাসা বেঁধে ছিল যাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন তো ছিলই, পাশাপাশি কম-বেশি স্বচ্ছলও ছিলেন। এইসব পরিবারের সদস্যরাই টাউনের সংস্কৃতির হাল ধরেছিলেন। তবে নীরদচন্দ্র চৌধুরী যেটা দেখিয়েছেন তা হলো, উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিরা একই সাথে দেশাত্মবোধের চর্চা এবং ইংরেজদের অধীনে কাজ করার কথা ভাবতেন। জলপাইগুড়ি টাউনের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হয়েছিল। ইংরেজদের কাছ থেকে বাঙালি ‘ফুটবল’ নামক একটা জিনিসও পেয়েছিল এবং টাউনে ফুটবল খেলার জন্য টাউন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা আর্যনাট্যেরও আগে।
১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরও জলপাইগুড়িতে তেমন কোন আলোড়ন ওঠেনি। মনে হয় বিষয়টি স্থানীয় মানুষের মনে তেমন ভাবে রেখাপাত করতে ব্যর্থ হয়। হতে পারে ‘টৌন জলপাইগুড়ি’র নবীনতা এবং ঐতিহ্যহীনতাই এর কারণ। কুচবিহার এবং বৈকুন্ঠপুর কখনোই বঙ্গ জীবনের অঙ্গ ছিল না। হতে পারে নবীন শহরের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বাংলাভাগ নিয়ে খুব একটা বিচলিত হন নি। এ নিয়ে অবশ্যই বিশদ গবেষণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু টাউনের স্বদেশী ইতিহাস গত শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে তেমন ভাবে দানা বাঁধেনি।
উনিশ শতকের একেবারে শেষে টাউন ছিল ছড়িয়ে থাকা বিরাট একটি গ্রামের মত। সেখানে প্রচুর সংখ্যায় ছিল রবার গাছ। ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের দাপটে তখন কম্পমান টাউন। বাবুদের বাড়ির মেয়েরা প্রকাশ্যে বের হতেন না। ইসলামপুর থেকে মালপত্র নিয়ে আসা গরুর গাড়িগুলি ভিড় করত বর্তমান কদমতলার কাছাকাছি রাস্তায়। বার্নেশ ঘাট থেকে মালবোঝাই নৌকো এসে থামত কিং সাহেবের ঘাটে। তিস্তার জল বছরে কয়েকবার ঢুকে পড়ত নিচু এলাকায়। সন্ধের আগে করলার কোন ঘাটে গা ধুতে আসা কোন ব্যক্তি নদীর ওপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা চিতাবাঘকে ধমক দিয়ে বলত ‘ভাগ ভাগ!’
দিনবাজারের নিকটবর্তী রেডলাইট এলাকা তখন থেকেই বিখ্যাত। আর টাউনের বাবুগিরির একটা অধ্যায় অনুষ্ঠিত হত সেখানে। নতুন টাউন, কাঁচা পয়সা, বাঈনাচ--- টাউনের ছোকরাদের বখে যাওয়ার কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এটাই সে যুগের হাওয়া। জগদীশ গুপ্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনের ঢোকার আগে যে বিরাট বেশ্যালয়টি ছিল, তা কখনো গুরুদেবের চোখে পড়েনি।
কিন্তু টাউনের কারো কারো চোখে পড়েছিল। সেই কারণেই না আর্যনাট্যের ভাবনা এলো!
(চলবে)
Have an account?
Login with your personal info to keep reading premium contents
You don't have an account?
Enter your personal details and start your reading journey with us
Design & Developed by: WikiIND
Maintained by: Ekhon Dooars Team